শুক্রবার, ২১ নভেম্বর ২০২৫, ০৮:৪০ পূর্বাহ্ন
বীমার ইসলামি দৃষ্টিকোণ
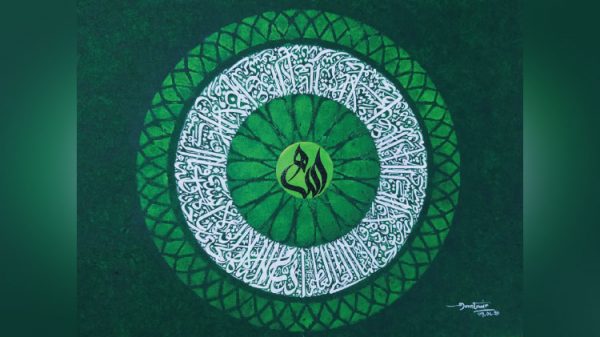 ইসলামী জীবন
ইসলামী জীবন শাহীন হাসনাত:
বীমা এমন একটি আর্থিক লেনদেনের চুক্তি, যাতে ভবিষ্যতে কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে তার ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নিশ্চিয়তার ভিত্তিতে কিস্তিতে নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত টাকা গ্রহণ করা হয়। যেসব দুর্ঘটনার ওপর বীমা করা হয়, সেদিকে লক্ষ রেখে বীমার তিনটি বড় বড় প্রকার রয়েছে-
সম্পত্তি বীমা : এর নিয়ম হলো, যে ব্যক্তি কোনো সম্পদের ওপর বীমা করতে চায়, সে নির্দিষ্টহারে বীমা কোম্পানিকে কিস্তি আদায় করে। যাকে প্রিমিয়াম বলা হয়। অতঃপর সেই সম্পদ দুর্ঘটনাগ্রস্ত হলে কোম্পানি তার আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। যদি সম্পদ কোনো প্রকারের দুর্ঘটনাগ্রস্ত না হয়, তাহলে বীমাকারী যে প্রিমিয়াম আদায় করেছে তা ফেরত দেওয়া হয় না। অবশ্য দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে বীমার টাকা বীমাকারী লাভ করে থাকে এবং তা দ্বারা সে নিজের ক্ষতিপূরণ করে। জাহাজ, গাড়ি, বাড়ি প্রভৃতির বীমা এর পর্যায়ভুক্ত।
ঝুঁকি বীমা : এর অর্থ হলো- ভবিষ্যতে কারও ওপর কোনো ঝুঁকি এলে সেটা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য বীমা করা। যেমন, মোটর গাড়ি চালানোর সময় কোনো দুর্ঘটনার ফলে কোনো অপর ব্যক্তির ক্ষতি হলে গাড়িচালক ওই ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য। কিন্তু এ ক্ষেত্রে বীমা করা থাকলে দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত তৃতীয় পক্ষকে ক্ষতিপূরণ আদায় করে বীমা প্রতিষ্ঠান।
জীবনবীমা : এর অর্থ হলো- কোম্পানি বীমাকারীর সঙ্গে এই চুক্তি করে, একটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তার (বীমাকারীর) অপমৃত্যু হলে বীমা প্রতিষ্ঠান চুক্তিকৃত প্রতিশ্রুত টাকা তার উত্তরাধিকারীদের আদায় করে দেবে। এর আবার কতকগুলো ধরন আছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মেয়াদ নির্দিষ্ট করা থাকে। সেই মেয়াদের ভেতরে মারা গেলে চুক্তির টাকা মৃত বীমাকারীর উত্তরাধিকারীরা পেয়ে যায়। যদি সে মেয়াদে তার মৃত্যু না হয়, তাহলে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর বীমাও শেষ হয়ে যায় এবং জমাকৃত টাকা সুদে-আসলে ফেরত পায়। পক্ষান্তরে কোনো কোনো ক্ষেত্রে মেয়াদ নির্দিষ্ট থাকে না। এরূপ হলে যখনই বীমাকারীর মৃত্যু হয়, তখনই তার টাকা তার উত্তরাধিকারীরা পেয়ে যায়।
কর্মপদ্ধতি এবং কাঠামোগত ও গঠনপ্রকৃতির দিক থেকে বীমা তিন প্রকার-
ক. গ্রুপ বীমা : সরকার এমন এক পথ ও পদ্ধতি অবলম্বন করে, যাতে জনসাধারণের কোনো একটি দল নিজেদের কোনো ক্ষতিপূরণ অথবা কোনো মুনাফালাভের ক্ষেত্রে সুবিধাভোগ করতে পারে। যেমন, সরকারি চাকরিজীবীদের বেতনের একটা অংশ প্রত্যেক মাসে কেটে রেখে বিশেষ ফান্ডে জমা করা হয়। অতঃপর কোনো চাকরিজীবীর মৃত্যু হলে অথবা সে দুর্ঘটনাগ্রস্ত হলে মোটা টাকা আকারে সাহায্য তার উত্তরাধিকারীকে অথবা খোদ তাকে প্রদান করা হয়। এটি একটি সামাজিক (সমাজকল্যাণমূলক) কাজ। যা সরকার দেশবাসীর সম্ভাব্য দুর্ঘটনার সময় অনুদানস্বরূপ দুর্গতদের সাহায্য করে। সুতরাং এটি সরকারের তরফ থেকে একপ্রকার অনুদান। কোনো বিনিময় চুক্তির ফলে বিনিময়ে অর্থ নয়। এ কারণে এই প্রকার অনুদান গ্রহণে কোনো প্রকার দ্বিমত নেই।
খ. সমবায় বীমা : এর নিয়ম হলো, যাদের সম্ভাব্য দুর্ঘটনা একই ধরনের হয়ে থাকে এমন কতকগুলো লোক পরস্পরে মিলে একটি ফান্ড তৈরি করে। অতঃপর তারা চুক্তিবদ্ধ হয়, চুক্তিকারীর মধ্যে কেউ দুর্ঘটনাগ্রস্ত হলে এ ফান্ড থেকে তার ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। এ ফান্ডে কেবল সদস্যদের টাকা জমা থাকে এবং ক্ষতিপূরণ কেবল এ সব সদস্যদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। শুরুর দিকে বীমার এই ধরনই প্রচলিত ছিল। যার বৈধ-অবৈধতার ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই। যে সমস্ত ইসলামি স্কলাররা বীমা নিয়ে আলোচনা করেছেন, তারা সবাই এর বৈধতার ব্যাপারে একমত।
গ. বাণিজ্যিক বীমা : এই বীমার নিয়ম হলো, কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করে বীমাকে বাণিজ্যরূপে পরিচালিত করা; যার মূল উদ্দেশ্য থাকে বীমার অসিলায় মুনাফা উপার্জন। এই কোম্পানি বিভিন্ন ধরনের বীমার স্কিম ঘোষণা করে। যে ব্যক্তি বীমা করতে চায় তার সঙ্গে বীমা কোম্পানির চুক্তি থাকে, এত টাকা এত কিস্তিতে আপনি আদায় করবেন। লোকসানের ক্ষেত্রে কোম্পানি আপনার ক্ষতিপূরণ দেবে। কোম্পানি কিস্তির পরিমাণ নির্ধারণ করার জন্য হিসাব করে, যে সম্ভাব্য দুর্ঘটনার ওপর বীমা করা হয়েছে তা কতবার হতে পারে? যাতে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার পরও কোম্পানির মুনাফা অবশিষ্ট থাকে। আর এই পরিসংখ্যান করার জন্য বিশেষ কৌশল আছে।
বর্তমানে এই ধরনের বীমার প্রচলন অধিক। এর বৈধতা-অবৈধতার ব্যাপারটি সাম্প্রতিক সময়ের আলেমদের মধ্যে বিশাল বিতর্ক লক্ষণীয়। মুসলিম বিশ্বের প্রায় সব ইসলামি স্কলারদের মতে তা অবৈধ। তাদের মতে, এই বীমাতে জুয়া ও সুদের সংমিশ্রণ আছে। জুয়া এ জন্য বলা হচ্ছে, টাকা আদায়ের ব্যাপারটা এক পক্ষের (বীমাকারীর) তরফ থেকে নির্দিষ্ট ও নিশ্চিত। কিন্তু অপরপক্ষের (কোম্পানির) তরফ থেকে তা সন্দিগ্ধ। বীমাকারী কিস্তিতে যে টাকা আদায় করে, তার সবটাই ডুবে যেতে পারে। আবার তার চেয়ে বেশিও পেতে পারে। আর একেই জুয়া বলা হয়। সুদ আছে এজন্য বলা হচ্ছে, এখানে টাকা দিয়ে বিনিময়ে টাকাই দেওয়া-নেওয়া হয়; যাতে কমবেশি হয়। বীমাকারী কম টাকা জমা করলেও পাওয়ার সময় তার চেয়ে অনেক বেশি পায়।
বীমা নিয়ে আরও বিস্তর আলোচনা-পর্যালোচনা রয়েছে। সেখানে মোটাদাগের বিষয়গুলো হলো- মানুষের প্রাণ বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শরিয়তের দৃষ্টিতে মূল্যমান সমৃদ্ধ কোনো পণ্য নয়। কাজেই তার মূল্য নির্ধারণ শরিয়তসম্মত নয়। প্রিমিয়ামের টাকা কোম্পানির কাছে ঋণ হিসেবে থাকে। যা নির্দিষ্ট শর্তে শর্তযুক্ত করা হয়। আর ঋণকে শর্তযুক্ত করা অবৈধ। অনেকক্ষেত্রে বীমায় প্রিমিয়াম কিছুদিন পরিশোধের পর বন্ধ করে দিলে তা আর ফেরত দেওয়া হয় না। যা শরিয়ত পরিপন্থী ও অমানবিক। তাছাড়া কোম্পানি প্রিমিয়ামের টাকা সুদের বিনিময়ে ইনভেস্ট করে। ফলে বীমাগ্রহীতার টাকার দ্বারা গোনাহে সহায়তা করা হয়, যা শরিয়তে নিষিদ্ধ।
আরেকটি বিষয়, প্রচলিত ইসলামি বীমা কোম্পানিগুলো তাদের প্রসপেক্টাসে যা উল্লেখ করে, তা শরিয়তসম্মত মনে হলেও তাদের কাজে তার বাস্তবায়ন খুব একটা দেখা যায় না। সাধারণ মানুষের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য ইসলামি পদ্ধতি ও শরিয়া বোর্ডের কথা বলা হলেও অনুসন্ধানে দেখা গেছে, বহুক্ষেত্রেই শরিয়া বোর্ডের কথা সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করা হয়। সবচেয়ে বড় ব্যাপার হলো, শরিয়ত সম্পর্কে অজ্ঞ যারা, তাদের মাধ্যমেই পরিচালিত হয় ইসলামি বীমা। শরিয়া বোর্ডে যে কজন আলেম থাকেন, তাদের গ্রহণযোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে।
ইসলামে এক কথায়- বীমা নিষিদ্ধ, বিষয়টি এমন নয়। তবে এর বাস্তবায়ন পদ্ধতি যদি অনৈসলামিক হয়, তাহলে ইসলাম তার বিরুদ্ধে। তাই সর্বসাধারণের কর্তব্য, বাস্তব অনুসন্ধানের পর বীমা কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত হওয়া।
লেখক : মুফতি ও ইসলামবিষয়ক লেখক
























